শ্যাঁকামালের মেলা
“কি গো ছোটমামী, মেয়েরা মেলায় আসবে তো?”
“কি জানি মা, কে কি করে। সবারই তো বাড়িতে কাজ। তোর মেয়েরা আসবে?”
“হ্যাঁ, বড়টা আসবে, ছোটটা হয়তো এবার পারবে না। মেজোমামী তোমার মেয়েরা?”
মেজোমামীও ওইরকমই একটা উত্তর দেয়।
মেলা চলার মাঝামাঝি পর্যন্ত এই চলে। কে এসেছে, কে আসবে।
এই গল্পের মামীরা হিন্দু, ভাগ্নি মুসলিম। কিন্তু মেলাটা মিলেমিশে সবার।
ছোট থেকে সেই মাঘ মাসের আট তারিখের অপেক্ষায় থাকতাম। দিন গুনতাম, আর কত বাকি। আনে-বালা পল যানে-বালা হ্যায়।কিন্তু সেসব আমাদের মাথায় থাকতো না। আগে তো আসুক, তারপর যাওয়ার কথা।
আমাদের গ্রামে ফকির পাড়ায় একটা মসজিদ আছে। সেটার আসল নাম হয়তো শাহ-কামালের মসজিদ। কিন্তু সবাই সেটা শ্যাঁকামালের মন্দির বলে। কেউ মসজিদ বলে না। ওটাকে ঘিরেই মেলা। প্রতি মাঘ মাসের সাত তারিখে ওই মসজিদটাকে পুরো দুধ দিয়ে ধোয়া হয়। বাজি পুড়িয়ে আনন্দ করা হয়। এটাকে বলে মাড়ো ধোওয়া। তারপর আট তারিখ থেকে মেলা শুরু হয়। পীরের গান আর যাত্রাও হয়। আগে টানা আট-নদিন যাত্রা হতো। এখন কদিন হয় জানিনা।
মসজিদের মাহাত্ম্য এতোটাই যে, সবাই সুখে-দুখে বাবা শ্যাঁকামালকে মানত করে বসে। জ্বর, জ্বালা থেকে শুরু করে যেকোনো রোগে। বা, পরীক্ষা ভালো হবে এই আশাতেও সবাই মনে মনে শ্যাঁকামালকেই ডেকে যায়। “বাবা শ্যাঁকামাল আমার যেন পরীক্ষা ভালো হয়, তাহলে তোমাকে এক টাকার বাতাসা দেব।” এই টাকার পরিমাণটা এখন নিশ্চয়ই বেড়েছে। যার যেমন সামর্থ্য তার তেমন মানত। কেউ ঘোড়া, কেউ জোড়া ঘোড়া, কেউ পীরের গান। কারো গরুর বাছুর না হলে সেও মানত করে বলে - বাবা শ্যাঁখামাল এবার বাছুর হলে তোমার মাড়ো ধোয়াতে এক পোয়া দুধ দেবো, কেউ কেউ আরো বেশি দুধেরও মানত করে থাকে। মানত কথাটাকে ওখানে সবাই বলে মানসিক।
পীরের গান আবার বার্ষিক মানতও হতো। যেমন, আমার ছোটঠাকুমা প্রতিবছর পীরের গান দিতো। মসজিদের কাছে সন্ধ্যেবেলা গানটা হয়। গান গাওয়ার জন্যে বাইরে থেকে একদল লোক আসে। দশ-বারো জন। তাদের মধ্যে একজন গায়ক থাকে, বাকিরা সঙ্গ দেয়। সঙ্গীরা গোল করে ঘিরে বসে, গায়ক তাদের মাঝখানে ঘুরে ঘুরে, হালকা নাচের চালে চামড় নেড়ে লাল আলখাল্লার মতো পোশাক পরে গান গাইত। মাথায় থাকতো একটা পাগড়ি। আর গান শোনার সময় কেউ পয়সা দিলে তার মাথায় চামড় বুলিয়ে আশীর্বাদ করতো। যারা যেদিন গান দিতো সেদিন গানের দল তাদের বাড়িতেই খেতো। সকালের চা, বিড়ি থেকে শুরু করে রাতের খাবার অব্দি। তার ওপর থাকে গানের ভাড়া। আগে সেটা দেড়শো-দুশো মতো ছিলো। পীরের পালাগান আমি কখনোই মন দিয়ে শুনিনি, তাই এখন আর কিছু মনে নেই।
গান শেষ হলে যাত্রা শুরু হতো। যাত্রার অনেক দল থাকতো। সবই গ্রাম আর পাশের গ্রাম মিলিয়ে। বড় দল, মাঝারি দল। কিসের ভিত্তিতে বড়, মাঝারির মাপকাঠি হতো আমার জানা নেই। তবে প্রথম দুদিন বড় দলের যাত্রা।
যাত্রা শোনার জন্যে আগে থেকে চাটাই পেতে জায়গা রেখে আসতে হতো। স্টেজের একদম সামনে জায়গা পাওয়ার জন্যে খুব ভোরে উঠেই চাটাই নিয়ে দৌড়তো সবাই। কেউ কারো চাটাই একটু সরিয়ে দিলে তা নিয়ে মারামারিও শুরু হয়ে যেতো। কেউ কেউ তো যাত্রা দেখতে গিয়ে পুরো ঘুমটা ওখানেই সেরে বাড়ি ফিরতো।
ঘোড়া আর বাতাসা মানত করতো যারা, তারা পীর পুকুরে চান করে দুপুরবেলা বা শুদ্ধ কাপড়ে সন্ধ্যেবেলাও মানত শোধ করতে যেতো। বাতাসা নেওয়ার জন্যে তখন মসজিদের পাশে বসে থাকতো আমিরন পিসি। পিসির হাতে ঠোঙাটা দিলে, পিসি মসজিদের সিঁড়িতে বাতাসাগুলো ঢেলে অর্ধেক নিয়ে বাকি অর্ধেক ঠোঙায় ভরে ফেরত দিতো। সঙ্গে মসজিদতলার ধুলোও দিতো। বাতাসার সঙ্গে ওই ধুলোটা খেয়ে সবাই মাথায় হাত মুছে নেওয়ার একটা চল ছিলো। বাতাসা মানতটা সারা বছরই লোকে করে থাকে। যখন ইচ্ছে হয় তখনই মানত মেটায়। কিন্তু গান আর ঘোড়াটা মেলার সময়ই দেয় সবাই। মানতের ঘোড়াটা তৈরি করে ময়রারা। মাটির ঘোড়া। ছোট থেকে বড়, যে যেটা মানত করতো সে সেটা কিনতো। ঘোড়াগুলো আর বাড়ি ফেরত আনতে হতোনা। ওই মসজিদতলাতেই স্তুপ হয়ে থাকতো। এখনো গেলে হয়তো দেখা যাবে।
পীর পুকুরে চান করলেও নাকি অনেক রোগমুক্তি হয়। তাই বহু গ্রামের মানুষকে ঝাঁকে ঝাঁকে চান করতে আসতে দেখেছি। আমাদেরকেও ছোটবেলায় মেলার সময় একদিন ওই পুকুরে চান করে আসতে বলা হতো। আর যাদের পুকুর নেই তারা তো সারাবছরই ওই পুকুরে চান করে। তবে তারা রোগে ভোগে না, এমন কথা আমি বলতে পারবো না।
আগে মেলায় জুয়া খেলা হতো। আমরা ওটাকে ডাইস খেলা বলতাম। হয়তো সেটা পাশা খেলার মতো। যাই হোক, কোনোটাই আমি খেলতে জানিনা। মেলার একপাশে ছোট একটা ঘর তৈরি করে খেলাটা চলতো। সেখানে ছোটদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। একবার ভুল করে উঁকি দিয়ে দেখেছিলাম। বড়জেঠু দেখতে পেয়ে খুব বকা দিয়েছিলো। ওই জুয়ার টাকা থেকেই মেলার পুরো খরচ আসতো। এখন কিভাবে হয় জানি না। তবে মেলা, যাত্রা, পীরের গান সবই চলে।
বড়রা মেলায় যাবার জন্যে পয়সা দিতো। আমরা দুহাত ভরে দু-ডজন কাঁচের চুড়ি, নাগরদোলনা, চপ-পাঁপড়-ঘুগনির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতাম। আমি নাগরদোলনায় উপরে উঠে যাবার সময় রুমাল নিচে ফেলে দিতাম, আবার নামার সময় মাটিতে হাত বাড়িয়ে কুড়িয়ে নিতাম। যে বছর নাগরদোলনা আসতো না, খুব মন খারাপ হতো। খুব ইচ্ছে করতো বন্দুক দিয়ে দেয়ালে সাজানো বেলুন ফাটাতে। কিন্তু সেটা শুধু ছেলেরা খেলতো, আমাদের কেউ খেলতে দিতো না।
ছোটবেলার আনন্দগুলোই আলাদা। একটা বাঁশি, লোডশেডিং চুড়ি, কাঁচের চুড়ি, নাগরদোলার মধ্যেই ঘোরে। চপ, পাঁপড়, গোলাপি রঙের জিবেগজা, জিলিপি। এখন বড় হয়ে ছোটবেলার আনন্দ হাতড়াই, একবার জিলিপির প্যাঁচ খুলে বেরিয়ে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করার কথা ভাবতে পারি না। অথচ ছোটবেলায় প্রতিদিন ওই পথ দিয়েই স্কুলে যাওয়া, স্কুল থেকে ফেরা। এতোটুকু ছাড়ার কথা ভাবতে পারতাম না। চেটেপুটে সবটুকুই উপভোগ করতাম।
ছোটবেলায় রচনায় লিখতে হতো মেলা মানে মিলন। এখন সেটা উপলব্ধি করি। সবার বাড়িতেই ওই কটাদিন আত্মীয় স্বজনেরা আসতো। নিয়ম করে সন্ধ্যেবেলা মেলা দেখা, রাতে যাত্রা শুনতে যাওয়া। যাওয়াটা থাকতো উপলক্ষ্য। গিয়ে গল্প করাটাই আসল। সবাই সবাইকে মেলায় খায়ানো। সে এক অন্যরকম ভালোলাগা।
পাঁজিপুঁথি দেখিয়ে মেলা শেষ হয়ে গেলেও রয়ে যেতো কিছু ময়রাদের দোকান। শান্তিদার মনোহারি দোকানের তাঁবুটা। আমরা ভাঙামেলাটাও বাদ দিতাম না। মেলা শেষ হয়ে গেলে পাশের গ্রামে খুব বন্ধু যারা তাদের বাড়িতে জিলিপি কিনে দিতে যাওয়ার একটা চল ছিলো। সবাই সেটা করতো। ময়রারা তাই আর একটু বেশিদিন থাকতো মেলায়। পীরের গানের মানত শেষ হলে মেলাও পুরোপুরি গুটিয়ে আর একটা মেলার জন্যে চলে যেতো।
স্কুল থেকে ফেরার সময় ভাঙা কাঁচের চুড়ির টুকরো কুড়িয়ে আনতাম। “চুড়িভাঙা” খেলার জন্যে।
এখন আর বাদল ময়রা, মলিনা পিসির মিষ্টির দোকানের উনানের গনগনে আঁচ, হাসি হাসি মুখে জিলিপি ভাজা দেখতে পাইনা। স্কুল ফেরত মেলা শেষের ধূসর ছাইগুলো, যেগুলো দেখে বুঝতে পারতাম কোনটা কার দোকান, এখনো সেগুলোই দেখি।
পৌষ পার্বণ, উঠোন লক্ষ্মীর পুজো এক এক করে সবই আসে। তারপর মিলেমিশে মেলাটাও হয় আনন্দের।
এখন আমি শুধু আর আট তারিখের অপেক্ষা করি না।
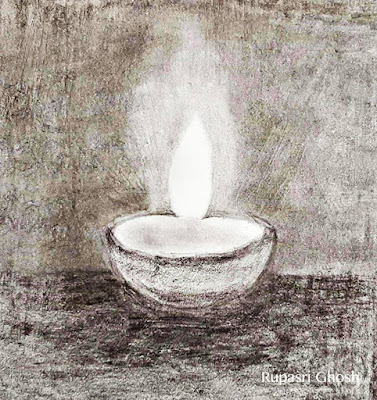
Comments
Post a Comment