স্কুলবেলা
বাবান স্কুল যাওয়া শুরু করেছে তার চার বছর দুমাস পাঁচ দিন বয়সে। প্রথম স্কুল, প্রথমদিন স্কুলে যাওয়ার খুশিটা বেশ দেখবার মতো ছিল। সবই অজানা, তাই কোনো উৎকণ্ঠা বা আশঙ্কাই ভিড় করেনি তার কচি মনে। কিন্তু প্রথমদিনের পর থেকেই শুরু হলো নানান বায়না। এক একদিনের এক একরকম। স্কুল থেকে ফেরার পর থেকেই শুরু হতে লাগলো কান্না — “কাল আমি স্কুলে যেতে চাই না”। চলতে লাগলো পরেরদিন স্কুলে ঢোকার আগে অবধি।
প্রথমদিন তিরিশ – চল্লিশ জন বাচ্চাকে সামলাতে ম্যাম ঠোঁটের উপর তর্জনী দিয়ে ইসসশ্চুপ বলে ইশারা করেছিলেন। সেটা বাবানের একেবারে পছন্দ হয়নি। সে সারাদিন বকবক করতে খুব ভালোবাসে। আমার মাথা পুরো খারাপ করে দেয়। দ্বিতীয় দিন স্কুল থেকে বেরিয়েই আমাকে বললো, “আমার স্কুল ব্যাপারটা ভালো লাগেনি।” বললাম কেন? বললো – “সেইইই না কথা বলা। শুধু চুপ করে থাকা।” এদিক ওদিক ঘাড় অব্দি ঘোরাতে পারেনি। ম্যাম নাকি মাথা ধরে ঘাড় সোজা করে দিয়েছিলেন। কথা যখন বলা বারণ তাই সে কথা বলেনি। কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিলো।
এরপর থেকে শুরু হলো প্রতিদিন হাজারো দুশ্চিন্তা!
“কাল আমাকে কি স্কুলে রঙ করাবে?” “তুলি দিয়ে? নাকি প্যাস্টেল?” “তুলি দিয়ে তো আমি রঙ করতে পারিনা”, বলেই একচোট কান্না। বললাম — ঠিক আছে শিখিয়ে দিচ্ছি। প্রবল উৎসাহ নিয়ে শেখা হলো। পেরে যাবার পর এবার দুশ্চিন্তা দিনক্ষণ নিয়ে – তুলি দিয়ে সত্যিই করাবে তো? করালে কখন করাবে? আবার কান্না। তোমরা চিঠি লিখে দাও আমাকে যেন রঙ করায়। সেদিন সকালে বুঝিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েই নতুন আশঙ্কা শুরু হলো আমার, কি জানি আজ ফিরে কোন ছুতোয় কাঁদবে।
আশঙ্কার জয়। সেদিন ক্লাসে গানের ম্যাম এসেছিলেন।
বললাম — তাতে কি হয়েছে? ভালো তো।
“না, তাকে আমার পছন্দ নয়। তোমরা লিখে দাও যে তাকে আমি চাই না।”
কেন? তিনি বকেছেন?
নাআআ।
তবে?
অনেক পরে বললো — ম্যাম কাছে ডেকে গান করতে বলেছে। ও গানটা নাকি এক রকম করে দিয়েছে, কিন্তু পেরেছে কিনা সেটা বোঝা গেলো না। সবথেকে বড় অভিযোগ — “তারপর আমাকে বলেছে — Go”।
অপমানের চূড়ান্ত। ‘Go’ বললো কেন? মনে পড়ে গেলো – ‘খাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ওলো বললো কেন?”
আরো অনুসন্ধান করে জানা গেলো, ম্যাম সবাইকেই কাছে ডেকে গান করতে বলেছিলেন। শেষে নিজের জায়গায় বসার জন্য ‘Go’ বলেছিলেন।
গানটা কি গান, বোঝার চেষ্টা করলাম। বারে বারেই উত্তর এলো ‘ভীষণা সং’। কিন্তু এমন ভীষণা সং তো কখনো শুনিনি।
এখনও বাবান ইংরেজিটা সব বুঝতে পারে না। কিছু বোঝে। সেটা ভেবে ‘ভীষণা সং’য়ের অর্থ খুঁজে বের করার চেষ্টা করলাম। বললাম — ম্যাম হয়তো বলেছেন – “We sing a song”. আমরা আসলে ‘উই’ বলি। ডব্লু এর যা উচ্চারণ তুমি তা বুঝতে পারোনি। ছেলে কিছুতেই মানতে রাজি নয়। তারপর মাথায় এলো —‘We shall overcome?’ তাও মানতে চায়না দেখে আমি গানটা বাজালাম। এটাই তার ম্যামের গান কিনা তা স্পষ্ট বোঝা গেলো না কিন্তু গানটা তার ভালো লাগলো। সারাদিন উঠতে, বসতে, শুতে গুণগুণ – ‘we shall overcome’। ভাবলাম যাক! বাঁচলাম। আমরা অন্তত overcome করেছি। কিন্তু নাআআ — আবার কান্না — কাছে ডেকে যদি অন্য গান করতে বলে, আর আমি না পারি, তখন তো ‘Go’ বলবে? আমি স্কুলে যাবো না! তোমরা লিখে দাও। আমরা একটু ধমকও দিতে শুরু করলাম, যে অমন সবকিছু লিখে দেওয়া যায় না। তুমি সবে নতুন যাচ্ছো, আস্তে আস্তে সব অভ্যেস হয়ে যাবে।
ছেলের বাবা ভাবলো সবকিছুতেই এমন বায়না করলে কি করে হবে? আমাদের ছোটবেলায় স্যাররা তো খুব কড়া ছিলেন, এমনকি ছড়ি দিয়ে মারতেনও। এখন তো তা হয় না। এদের তো অনেক ভালো বরং। আমরা অমন কথায় কথায় কাঁদতাম না। এ কথায় আমার একটু আপত্তি। আমাদের ছোটবেলা আর ওর ছোটবেলা তো কোনো অঙ্কেই মেলে না।
আমাদের প্রাইমারী স্কুলের জীবন ছিল একেবারে আলাদা। আমরা স্কুলে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে থাকতাম, কখন পরেরদিন গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে হই হুল্লোড় করতে পারবো সেইজন্যে। ওই বয়সে নিয়ম মেনে পড়ার কোনো গল্পই ছিলো না। শিশুশ্রেণিতে তো যে যা খুশি তাই। স্যারদের কোনোদিন যদি ইচ্ছে হতো তাহলে এক এক করে তুলে বলতেন ‘পড়া বল’। সেই – অজ, আম, চারি, পূজা। তারপর ‘জল পড়ে পাতা নড়ে’ এসে গেলে মনে হতো উফ কি বড় হয়ে গেছি। বর্ণপরিচয় এর দ্বিতীয় ভাগ পড়তে পারলে তো কথাই নেই! মাঝে মধ্যে শ্লেটে নিজের নাম, বাবার নাম, স্কুলের নাম, বা ঠিকানা লিখে দেখানো। সেটাও রোজ নয়, স্যারদের যদি মনে হতো এদের একটু ব্যস্ত রাখি, তবে।
ছুটির জাস্ট আগে কোনো কোনো দিন সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে সুর করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নামতা পড়া – এক এক্কে এক, দুই এক্কে দুই দিয়ে শুরু করে কুড়ির ঘর অব্দি। ক্লাস ফোর মানে তারা হিরো, তাই তাদের মধ্যে একজন বলতো তারপর সবাই সেটা চেঁচিয়ে — হুক্কাহুয়া করার মতো। স্যাররাও সেই সময় স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্যে। যেই শেষ হতো, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই একজন ছুটির ঘন্টা বাজিয়ে দিতো। তারপর সব হুড়মুড় করে লাফাতে লাফাতে দৌড়। “ছুউউউটিইইই, গরম গরম রুউউটিইই” বলতে বলতে।
বাবানদের স্কুলে বাবানরা এমন হৈ হৈ করে বেরোয় না। তাদের দারোয়ান ছুটির ঘন্টা দেয়। তারপর প্রথমে নার্সারির বাচ্চারা একে অপরের কাঁধ ধরে লম্বা রেলগাড়ি করে বড় বিল্ডিং এ যায়। সেটা দেখতে বেশ লাগে। এয়ারপোর্ট বা সুপারমার্কেটের ট্রলিগুলো একসঙ্গে যখন কেউ নিয়ে যায়, অনেকটা সেই ধরনের। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো কেউ কাউকে ছাড়ে না। তারপর সেখানে – এ থেকে যতগুলো সেকশন আছে সবাই আলাদা আলাদা লাইনে দাঁড়ায়। হয়ে গেলে, বাবা- মা’দের বলা হয় লাইন দিতে। এরপর এসকর্ড কার্ড দেখিয়ে বাচ্চাকে নেওয়া। এইভাবে এল কে জি, ইউ কে জি, ওয়ান সব একই নিয়ম। তার মধ্যেই একটু দেরি হয়ে গেলে অনেক বাচ্চা দূর থেকে মাকে, বাবাকে দেখে কেঁদে দেয়। এরমধ্যে আবার বাস চিলল্ড্রেন, প্রাইভেট চিল্ড্রেনের একটা গল্প আছে। বাস চিল্ড্রেনদের আগে যেতে দেওয়া হয়। বাবান এটার মানে বুঝতো না বলে তাই নিয়েও কান্নাকাটি করেছে। ওদের কেন আগে যেতে দেওয়া হয়? ছুটির পরে ও ক্লাস থেকে বেরোতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বাস চাইল্ড নয় বলে নাকি ওকে একদিন ম্যাম ক্লাসরুমে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তারপর তাকে এটা বোঝানো হলো, বাস চিল্ড্রেনরা অনেক দূরে যায় তাই আগে যেতে দেওয়া হয়। প্রাইভেট চিলড্রেনরা তো বেরিয়েই মা বাবাদের পেয়ে যায়। সেটা বুঝেই শান্ত হয়েছে। তারপরেও তার দাবি — মা বাবাদেরও তো লাইন দিতে হয়, সেই লাইনেও তোমাদের ফার্স্ট হতে হবে। বাবা একদিন অনেক মা’দের ভিড়ের মধ্যে না গিয়ে ধীরে সুস্থে একটু দেরি করে লাইনে গেছিলো। বাবান ক্লাসরুম থেকে বেরিয়েই কাউকে দেখতে পায়নি। ওর কান্না পেয়ে গেছিলো — কিভাবে বাড়ি যাবে?
আমাদের শুধু গরমকালে দুমাস মতো মর্নিং স্কুল হতো। খুব সকালে, ছটা থেকে দশটা। সে আর এক আনন্দ। টিফিন নিয়ে যেতে পারবো। ডে স্কুলে টিফিনে বাড়িতে ভাত খেতে আসতে হতো, খুব বিরক্ত লাগতো। বাড়ির কাছেই স্কুল। খেলা কম পড়ে যেতো। মর্নিং স্কুলে খুব মজা পেতাম। লাল্টুর ভাই পল্টু, বৌ বসন্ত, রুমাল চুরি, খো খো সব খেলা। তারপর এক ফাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে চৌধুরীদের আমতলা, পদ্মাপিসিদের মিষ্টি তেঁতুল গাছতলাও ঢুঁ মারা যেতো।
বাবানদের স্কুল সাড়ে আটটা থেকে বারোটা। ওদের রোজই টিফিন দিতে হয়। আজকালকার বাচ্চাদের খাওয়া নিয়ে কোন ভরসা নেই, তাই যে বাচ্চা পুরো টিফিন খাওয়া শেষ করে, ম্যাম তার হাতে বড় করে স্মাইলি এঁকে দেন। স্মাইলির লোভে কোনো কোনো বাচ্চা পুরো টিফিন খেয়ে নেয়। বাবানের হাতের স্মাইলির দাগ মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আর একটা স্মাইলি মিলে যায়। সে সেটা খুব যত্ন করে রেখে দেয়, সাবান দিয়ে তুলতে দেয়না। টিফিনে নিয়ে যায় শুধু নুন দিয়ে সিদ্ধ পাস্তা আর সিদ্ধ ডিমের সাদা, কুসুমও নয়। এর কোনো ভ্যারিয়েশনই চলবে না। অন্য কোনো খাবারও না। হাজার বুঝিয়েও না। ‘আমার ওটাই ভালো লাগে, তোমরা আমাকে ওটাই দেবে’। ম্যাম তাই ওকে একদিন বলেছেন — ‘আজকেও পাস্তা? I will call you a pasta boy.’
ওদের স্কুলে টিফিন দেবার আবার কিছু নিয়ম আছে। অনেক মা বাবা টিফিন দেওয়ার নিয়মে উল্টোপাল্টাও করে থাকেন। একদিন ছেলেকে স্কুল থেকে আনতে গিয়ে দেখলাম একজন ম্যাম মাইক্রোফোন নিয়ে বাবা – মা’দের খুব বকাবকি করছেন। শুনলাম কেউ আলুপরোটা, কেউ বিরিয়ানি কেউ বা ফ্রায়েড রাইস দিয়েছিলেন টিফিনে।
আমরা যা খুশি তাই করতাম। বন্ধুদের মধ্যে জিনিস দেওয়া-নেওয়াও চলতো। খাবারও আমরা ভাগ করে খেতাম। এমনকি স্যারদেরও বাড়ি থেকে খাবার এনে দিয়েছি মাঝে মধ্যে। কেউ কেউ তাদের গাছের আম, কলা, লেবু, কেউবা চাষের সবজি, পুকুরের মাছও এনে দিতো। গ্রামে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার।
বাবানদের স্কুলে একটু অন্যরকম। সবার জন্য এক নিয়ম। দেওয়া নেওয়া বন্ধ। একমাত্র যার জন্মদিন সে শুধু সেইদিন, বা পরেরদিন নিয়ম মেনে ক্লাসের সব বন্ধুদের জন্য একলেয়ারস নিয়ে যেতে পারে। তার বেশি কিছু নয়। সবার স্কুলে এক নিয়ম নয়। আমাদের কলিগ বা অন্যবন্ধুদের কাছে শুনেছি তাদের বাচ্চাদের স্কুলে যে যা খুশি গিফট নিয়ে যেতে পারে। তাতে বাবা- মা’রা একটু সমস্যায় পড়ে, কি কিনবে সেটা ভেবে। বাবানদের স্কুলের নিয়মটা সে অর্থে ভালোই বলা যায়। ওদের শেয়ার করা ব্যাপারটা ম্যামরাই শেখান। একে অপরকে টিফিন দিতে শেখা। তবে সেটা রোজ নয়। মাঝে মধ্যে। কোনো কোনো দিন ডায়েরিতে লিখেও দেন টিফিন ছাড়া অন্য খাবার কি কি পাঠাতে হবে।
একদিন যেমন ‘নো ফায়ার কুকিং’ এর জন্যে বেদানা, শশার কুচি আর আলুর চিপসের প্যাকেট দিতে হয়েছিলো। এই কম্বিনেশনে আমরা একটু থ হয়ে গেছিলাম। কি করাতে পারেন সেটা ভেবে। ভেবে পাইনি। ছেলে এসে বললো আজ চিপস পার্টি হয়েছে। তাতে চাট মশালা ছড়িয়ে দিয়েছিলো। চার্ট মশালা অন্য স্টুডেন্টরা এনেছিলো। চিপসের উপর চার্ট মশালা….. যাক গে … মনে হয় সেও এক মজার ব্যাপারই হবে। বেদানাটা আলাদাই খেতে বলেছিলেন।
আমি প্রাইমারী স্কুলের গোটা পাঁচ বছরের জীবনে মার খেয়েছিলাম মাত্র একবার। আমার ভুলে নয়। এক স্যার রোজ ঘুমোতেন। সেদিন ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচিতে তাঁর ঘুম ভেঙে গেছিলো। তখন তিনি ছড়ি হাতে দৌড়ে এসে সবাইকে একধার থেকে শপাং শপাং করে মেরেছিলেন। আমি সেদিন চেঁচাইনি। তবু ঐ ঝাঁকের মধ্যে ছিলাম বলে মার খেয়েছিলাম। খুব লেগেছিলো। কষ্টও পেয়েছিলাম। ঐ স্যারকে কেউই খুব একটা পছন্দ করতো না। আমিও না। উনি এলেই সবাই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতো। ঘুমোনোর সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বলতেন হাওয়া করতে। পড়ানোর সময়ও। তালপাতার হাত পাখা দিয়ে হাওয়া করতে হোতো। আমাকে একবার পড়া দেওয়ার সময় হাওয়া করতে হয়েছিল। উনি চেয়ারে বসে টেবিলে পা তুলে ঘুমোতেন। পড়া দেওয়ার সময় টেবিলের চারপাশে সবাইকে বই নিয়ে গোল করে দাঁড়াতে হতো। যাকে পড়া ধরতেন সে বলতো। পড়া দেওয়ার সময় উনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে, সেদিন আমি সাহস করে পাখাটা টেবিলে খুব জোরে জোরে ঠুকে ওনার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি থতমত খেয়ে উঠে পড়েছিলেন। আমার ভাগ্য ভালো ছিলো। সেদিন মার খাইনি।
আমাদের স্কুলে কয়েকটা মোটে বেঞ্চ ছিলো। তাতে ফোরের ছেলেমেয়েদেরই বসতে দেওয়া হতো। সেটা শুধু বসারই, হাইবেঞ্চও ছিল না। কিছু সরকারি চটের আসন ছিলো। তাতে সবার হতো না। বাকিরা বাড়ি থেকে আসন নিয়ে যেতো। বাবানদের স্কুলে সবার জন্যই আলাদা আলাদা চেয়ার। সামনে বই রাখার ডেস্ক। মাথার উপর পাখাও ঘোরে। টিভি দেখিয়ে ছড়া শেখানো হয়।
আমাদের স্কুলড্রেসের কোনো গল্পই ছিলো না। যা খুশি তাই জামা পরে যেতে পারতাম। একটা নতুন জামা পেলে মনে হতো পরেরদিন কখন বন্ধুদের দেখাতে পারবো। আর তখন স্কুল থেকে এক ধরনের ড্রেস দিতো। মেরুন কালারের একটা ফ্রক। সেটা সবাই পেতো না। শুধু গরীবদের দেওয়া হতো। আমার খুব ইচ্ছে করতো ওই জামাটা পেতে। ছোটবয়সে সব ছেলেমেয়ের জন্যই বোধ হয় এক নিয়ম হলে ভালো হয়। এখনকার বাচ্চাদের স্কুলে ড্রেস থেকে শুরু করে টিফিনের এক নিয়মটা মনে হয় এই কথা ভেবেই। বাচ্চাদের মনে আর্থিক বৈষম্যটা না ঢোকানোই ভালো। স্কুলের এই সাম্য বজায় রাখাটার দুটো কারণ হতে পারে। এক – বই থেকে শুরু করে জামা জুতো অব্দি তাদের থেকে কিনলে তাদের আয় বাড়লো। আর এক – তাহলে কোনো ছেলেই এর ওটা ভালো, আমার এটা খারাপ ভাবার সুযোগটাও পায়না। আমি বাবানকে আনতে যাওয়ার সময় তার টুপিটা নিয়ে যাই। বেরিয়ে সে ওটা মাথায় দেয়। একদিন ওর ক্লাসেরই একজন, অমন টুপি চাই বলে খুব বায়না করেছিলো।
আমাদের সময়ে প্রাইমারী স্কুলে পাঁউরুটি দেওয়ার একটা চল ছিলো। রোজ নয়, মাঝে মাঝেই। একটা টাক মাথা লোক, সাইকেলের পিছনে বস্তায় করে নিয়ে চলে আসতো। সেখান থেকে গোটা কুড়ি আমাদের স্কুলের জন্য বরাদ্দ। এক একটা লম্বা এক পাউন্ড সাইজের। পিস করা থাকতো না। স্যাররা ছুরি দিয়ে কেটে পিস করতেন। এক একদিন এক একজন, স্যার যাকে ডাকতেন, সে গিয়ে সবাইকে দিয়ে দিতো। আমাকেও মাঝে মধ্যে দিতে হয়েছে। যে দিতো, নতুন মাস্টার তার পিসটা একটু বড় রাখতেন। সেটা আমার কাছে কোন লোভের ব্যাপার হবার কথা ছিল না, কারণ তখন আমি পাঁউরুটি খেতাম না। তবুও বড়টা পেতে ভালোই লাগতো। কত ছোট ছোট জিনিসেই তখন আনন্দ খুঁজে পেতাম। এখন বাবানও স্মাইলি পেয়ে যেমন খুব খুশি হয়।
এই নতুন মাস্টারমশাই স্কুলে অন্যদের তুলনায় নতুন। সবাই নতুন মাস্টার-ই বলতো। উনি খুব ভালো ছিলেন। আমাকে খুব ভালোবাসতেন। একেবারেই মেয়ের মতো। তাঁর টিফিন আমাকে খেতে দিতেন। শুকনো মুড়ি, তেল, চানাচুর মেশানো। তাই একসঙ্গে খেতে অসুবিধাও হতো না। স্যার কিছুতেই আমাকে মারতেন না, পড়া ভুল করলেও না। ওই বয়সে মার না খাওয়া মানে, বন্ধুদের সামনে লজ্জায় না পড়া। সেখান থেকে নতুন মাস্টারকে ভালো লাগারই তো কথা। খুব ভালো লাগতো আমার।
বাবানেরও এরই মধ্যে একজন খুব পছন্দের ম্যাম হয়েছেন। বাবান শুরুতে তাকে পছন্দ করতো না। রাগী ম্যাম ভাবতো। ইনিই কথা বলতে বারণ করেছিলেন। একদিন ম্যামরা জিজ্ঞেস করেছিলেন কে কে ব্রেকফাস্ট করে এসেছো? বাবান বলেছিলো আমি করিনি। রোজ যা খেয়ে যায় সেদিন সেটা না খেয়ে অন্যকিছু খেয়েছিলো। তাই ওটা ওর ব্রেকফাস্ট মনে হয়নি। তাই শুনে ওই ম্যাম বলেছিলেন – ‘আহারে ছেলেটাকে খাইয়ে পাঠায়নি।’ ব্যাস! সেটা বাবানের খুব ভালো লেগেছিলো। ফিরে এসে বলেছিলো – ‘মা ওটা আদর তো নাকি?’ বলে ম্যামের কথাটা নকল করে দেখানো হয়েছিলো। ঐ ম্যামই ওকে pasta boy বলেছিলেন। মাঝে মধ্যেই ম্যামকে নকল করা হয়। চোখগুলো ছোট ছোট করে, শান্ত গলায় একটু নিচু স্বরে আমাকে বলে – ‘ডোন্ট টক, ফিনিশ ইওর টিফিন।’
ইস্ত্রি করা জামা, প্যান্ট, এপ্রোন, ন্যাপকিন, পালিশ করা জুতো, সাদা ধবধবে মোজা। টিচার – প্যারেন্ট বার্তা দেওয়া নেওয়ার জন্য ব্যাগে ডায়েরি। গলায় আইকার্ড ঝুলিয়ে লাইন দিয়ে ঢোকা, এসকর্ড কার্ড দেখিয়ে ছেলে – মেয়েকে ফেরৎ নেওয়া, এমনকি জলের বোতলটা কেমন হবে সেটাও নিয়ম মেনে কিনতে হিমশিম খাওয়া। টিফিন দেওয়ার ব্যাপারেও তাদেরই নিয়ম মানা। এসব আমাদের বাবা-মাদের পোহাতে হয়নি ঠিকই। তবুও স্কুল থেকে ফেরা না অব্দি তাদের চিন্তাও কোনো অংশে কম ছিলো না।
বাবানের এখন গরমের ছুটি চলছে। এখন তার স্কুল যেতেই ভালো লাগে। বলেছে ‘প্রথম প্রথম ওরকম সবারই দুঃখ হয়, কষ্ট হয়। তোমাদেরও হয়েছিলো।’ ছুটিতে সারাদিন বাড়িতে সে হাঁপিয়ে উঠছে। একটু খেলা কম পড়ে গেলেই বলছে- ‘আমার তো স্কুল নেই, আমি তো তোমারেই বাচ্চা, তাহলে আমার সঙ্গে কে খেলবে বলো?’ শুধু তাই নয়, এই মুহূর্তে তার একটা ভীষণ দুঃখও শুরু হয়েছে। স্কুল খুললেই LKG থেকে UKG হয়ে যাবে না তো? কারণ সে UKG তে যেতে চায়না। LKG তে যে দুজন ম্যাম পড়ান তাঁদের এবং কয়েকজন ক্লাসমেটকে তার ভীষণ পছন্দ হয়েছে। UKG তে চলে গেলে তাদের সঙ্গে যদি আর দেখা না হয়। ওর সঙ্গে তারাও পরের ক্লাসে যাবে এটা বুঝিয়ে কোনো কাজ হয়নি। এমনকি সে বলে দিয়েছে অন্য কোনো স্কুলে, অন্য কোনো ক্লাসেই সে যেতে চায় না। ঐ LKG তে, ঐ সেকশনেই সারাজীবন পড়বে।
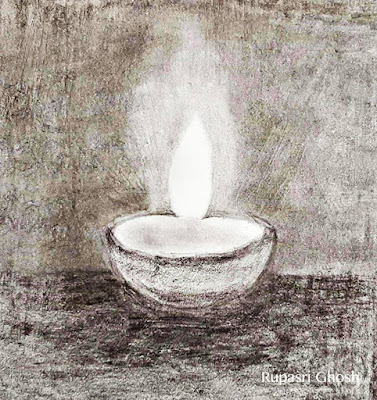
Comments
Post a Comment