নববর্ষ
সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়েই দেখতাম পুকুরে জাল দেওয়া হচ্ছে। কারণটা জানার আগেই এক দৌড়ে ছুট্টে চলে যেতাম পুকুর পাড়ে। পাড়ে দাঁড়িয়ে ভীড় করে থাকতো আরো অনেকে। দাদারা, জেঠুরা, কাকারা, জ্যাঠতুতো দাদারা ছাড়াও পাড়ার অনেকে। কেউবা মাছ কিনতে, কেউবা আসতো চাইতে। এটা পুকুরে জাল দেওয়ার দিনগুলোর চেনা ছবি হলেও, পয়লা বৈশাখ যেন একটু বেশিই ভীড় হতো। তার মধ্যে মহামায়া ঠাকুমার হাজিরা ছিলো নিশ্চিত। যেখানে যার পুকুরেই জাল দেওয়া হোক না কেনো, সে ঠিক হাজির হয়ে যেতো। বলতো আমাকে একটা মাছ দেনা বাবা, আমার বুড়ো মা’টা না হলে খেতে পাবে না। আড়ালে মহামায়া ঠাকুমাকে সবাই ‘মহা বাউনি’ আর তার মাকে ‘শুটকি বাউনি’ বলতো। তাদের নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টাও করতো। ব্রাহ্মণ বাড়ির দুই বিধবা। মা আর মেয়েতে ছোট্ট সংসার। চেয়ে চিনতেই দিন চলতো, আয় বলতে নিজের গ্রাম আর পাশের গ্রাম মিলে মাত্র কঘর যজমান। তার মা সত্যিই খুব জীর্ণ ছিলো। শরীরে হাড় কখানা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। সবাই মহা-ঠাকুমাকে দেখলেই বলতো, ওই চলে এলো চাইতে। অন্য দিন যে খাবার চেয়ে এনে চালায় পয়লা বৈশাখ সে তো চাইবেই।
পুকুরের ধারে জালটা যখন ছোট হয়ে গুটিয়ে আসতো তার মধ্যে চকচকে রুপোলী রঙের রুই, কাতলা, সিলভার কার্প, ফলুই লাফালাফি করতো সেটা দেখতেই আমার দারুণ লাগতো। অনেকে পাড়ের কাছে আসা মাছগুলো ধরার চেষ্টা করতো। মাছ ধরা দেখতে আমার খুব ভালো লাগে। মাছে হাত দিতে ঘেন্না লাগে। খেতেও খুব একটা পছন্দ করিনা। আজও তাই। এর মাঝেই জ্যাঠতুতো দাদা আমাকে বলে দিতো একটু পরে চান করে চলে আসিস দোকানে।
মেজোজেঠুর মুদির দোকান। দোকানে পয়লা বৈশাখ পুজো হয়। জেঠু বলতো কাল হালখাতা আছে, পুজোর জোগাড়টা করে দিস। সকালবেলা চান করে আমি আর জেঠুর মেয়ে মৌসুমিদি, ফল কাটা বঁটি নিয়ে হাজির হয়ে যেতাম। এত্তো ফল কাটতে হতো। কারণ দোকানের বাঁধা খদ্দের যারা তাদের বাড়ি বাড়ি ফল পৌঁছে দেওয়া ছাড়াও অনেকে এমনিই আসতো পুজোর প্রসাদ খেতে। ফল কাটার দিকটা আমরা সামলাতাম, আর নতুন খাতাটা সাজাতো জাঠতুতো দাদা। লালসালু কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা নতুন খাতার প্রথম পাতায় তেল দিয়ে গোলা লাল সিঁদুরে লেখা হতো “ওঁ শ্রী শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ”। তার নিচে গোল করে পাকানো মাথা, দুহাত তোলা, দুটো পা নামানো গণেশের প্রতীক, স্বস্তিক চিহ্ন আর ওই গোলা সিঁদুরে চোবানো একটাকার একটা কয়েনের ছাপ। দোকানের চৌকাঠের মাথাতেও সিঁদুর দিয়ে ওই একই কথা লেখা হতো। আর দড়িতে ফুল,আমপাতা, বেলপাতা গেঁথে মালার মতো করে গোটা দোকান সাজানো। দোকানের চার কোণায় পোঁতা হতো ঘটসহ চারটে কলাগাছ। পয়লা বৈশাখ পুজোর পর থেকেই নতুন খাতায় চালু হতো নতুন বছরের হিসাব নিকাশ। পুজোর সময়ের ধুনোর ধোঁয়া আর গন্ধ আজও আমার নাকে আসে। পুজোর সব প্রসাদ শেষ হওয়ার আগে জেঠু মনে করিয়ে দিতো মহা- পিসির জন্য যেন প্রসাদ থাকে, সে একটু পরেই আসবে। জেঠুর মহা-পিসি আসলে মহামায়া ঠাকুমা। পুজো শেষে আমার দুপুরের খাওয়া বরাদ্দ ছিলো জেঠুর বাড়িতেই। সেটা একটা মহা আনন্দের বিষয়। রোজকার নিয়ম ভেঙে একটা নতুন কিছু মানেই বোধহয় সবার মনে একই আনন্দ বয়ে আনে।
বিকেল হলে দফায় দফায় বাড়িতে আসতো – লাঠি ধরে, কোমর পড়ে নুয়ে যাওয়া, কালো গোল ফ্রেমে, মোটা পাওয়ারের না মোছা চশমা পরা দাদু রাম হাড়ি, তার বোন সরস্বতী ঠাকুমা, রাম দাদুর নাতির হাত ধরে তার বৌমা। এরা আমাদের ধাইমার বাড়ির লোক। বিশে নাপিতের মা, আমাদের ধোবি বাসু কাকার মা। মহামায়া ঠাকুমা তো আছেই। সবাই এসে একটু গল্প করে যেত আর তাদের পাওনা চাল, মুড়ি, চালভাজা, খই, মুড়কি নিয়ে যেতো। এদের জাত কাজ বন্ধ হয়ে গেলেও পাওনাটা নিয়ে যেতো। এরা আমাদের পরিবারের একজন হিসেবেই গণ্য হতো যেকোনো অনুষ্ঠানে। এদের উত্তর পুরুষরা আজ আর এসবের ধাত ধারে না। সবাই মোটামুটি খেটে খাওয়ার চেষ্টা করে। আর সব থেকে বড় কথা তখন বাড়িতে মুড়ি, চালভাজা, খই ভাজা হতো, মুড়কি তৈরি হতো। আজ তা ইতিহাস। এখন সবাই গ্রামে থাকলেও মেশিনে ভাজা মুড়ি কিনে এনেই খায়। চালভাজারও একটা বিশেষ ধরণ ছিলো। সবার ভাজা সমান হতো না। আমার ছোটঠাকুমা আবার ভাজতো একটু স্পেশাল করে, বিভিন্ন মশলা মিশিয়ে, ছোলা, বাদাম ভাজা মিশতো তাতে। আমি কোনোকালেই এসব খেতে ভালোবাসতাম না। অঢেল ছিলো বলেই বোধ হয়। আলস্যও প্রশ্রয় পেতো। কষ্ট করে চিবিয়ে খাওয়া ভাবতেই পারতাম না। আজ কংক্রিটের শহরে বসে সত্যিই সেই গন্ধগুলো মিস করি। যদিও আজ গ্রাম – শহরের খুব একটা তফাৎ আছে বলে মনে হয় না, তবুও..!
মনে মনে সন্ধেবেলার কথা ভেবে আরো আনন্দ পেতাম। সন্ধেবেলা দাদারা বাড়ি ফিরবে যখন, তখন হাতে থাকবে সরু রোল করে পাকানো গার্ডার দিয়ে মোড়া বাংলা ক্যালেন্ডার আর একটা করে ছোট মিষ্টির প্যাকেট। মিষ্টি খাওয়ার থেকে প্যাকেটে কোন দোকান কি দিয়েছে সেটা দেখাতেই উৎসাটা থাকতো বড্ড বেশি। আর ক্যালেন্ডারে ছবি কাদের বেশি ভালো হয়েছে, কাদের ক্যালেন্ডার এর কাগজটা বেশি ভালো, কাদের ওয়েল পেন্টিং। তলায় দোকানের নামটা লেখার স্টাইল নিয়েও চলতো বিপুল আলোচনা। অনন্ত টেলার্স, গোপাল খাঁড়া বস্ত্রালয়, দে টোর্স, হীরা ফার্মেসি।
প্রতি পয়লা বৈশাখে আমার যার কথা মনে পড়ে সে আমার প্রিয় বন্ধু হাসিবা। আমাদের পাশের গ্রামে আমার এক পাতানো দাদু আছে। ওই দাদুর কোনো মেয়ে নেই, তাই আমার মাকে মেয়ে পাতিয়েছে। ওই মামাবাড়ি আমার নিজের মামাবাড়ির থেকেও বেশি। দাদুরও মুদির দোকান ছিলো। একবার পয়লা বৈশাখে বিকেলবেলা আমি দাদুর পাশে বসে হালখাতা করা দেখছিলাম। হালখাতা মানেটা তখন আমি বুঝতাম না, দাদু বুঝিয়ে দিয়েছিলো। দেখতে আমার খুব আনন্দ লাগছিলো। এক এক করে সব লোক আসছে, টাকা দিচ্ছে। তাদের হাতে একটা করে ক্যালেন্ডার আর মিষ্টির প্যাকেট ধরানো হচ্ছে। আমার মজা দাদুর কত টাকা হচ্ছে। ওই টাকাটার মানেও তখন বুঝতাম না! ওইভাবে টাকা দেওয়ার সময় দেখলাম আমার বয়সী একজন, খুব ফর্সা, ববকাট চুল, গজ দাঁত, হাতকাটা মেরুন কালারের জামা পরে মিষ্টি দেখতে একটা মেয়ে। দুজনে দুজনের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে ছিলাম। পরের বছর প্রাইমারি স্কুল শেষ করে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হতে গিয়ে আবার সেই মেয়েটার সঙ্গে চোখাচোখি। হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। সে মিষ্টি হেসে বলেছিলো খাঁড়াদের দোকানে হালখাতা করতে গিয়ে তোমাকে দেখেছিলাম। তারপর এক ক্লাসে, এক বেঞ্চে, কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে বসা। কোনোদিন যদি দুজনের একজন কামাই করতো তাহলে অন্যজনের অসহায় অবস্থা নিয়ে ক্লাসের বাকিদের ঠাট্টা থেকে রেহাই পেতাম না। আজ সে হাসিবার কোনো খবরই আমার জানা নেই। সে ফেসবুকের মুখ দেখেনি। তার ফোন নম্বর আমি জোগাড় করতে পারিনি। সে দুই সন্তানের মা হয়ে ঘোরতর সংসারী, শুধু এটুকু তথ্যই আমার সম্বল।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাসিবার মতো সবই কেমন হারিয়ে ফেলেছি। আজ চাইলেও পুকুর পাড়ে দৌড়ে যেতে পারি না। সেই পুকুরে আর আগের মতো মাছও চাষ হয় না। বাড়িতে মুড়ি, মুড়কি, চালভাজার গন্ধও পাইনা। জেঠু, ছোটঠাকুমা, মহামায়া ঠাকুমা সবাই অতীত। গ্রামেও কংক্রিটের রাস্তা, সারি সারি ইটের বাড়ি, সুইচ টেপা জল। বৃষ্টি হলেও সোঁদা মাটির গন্ধ আমাকে সব ভুলিয়ে দেয় না। আর আরো ছোটবেলায় ফিরে গিয়ে যাঁকে সবসময় খুঁজি — শুধু পয়লা বৈশাখ নয়, যাঁকে ক্লাস ফাইভেই হারিয়ে ফেলেছি — যাঁর কাছে আর কোনোদিন নতুন জামা চাইতে পারিনা, পারবো না! ‘নববর্ষ’ কথাটা লিখতে গেলে যাঁর নাম আগে আমার মাথায় আসে তিনি আমার বাবা। নবকুমার।
আজ সকালবেলা আমার ছেলেকে যখন বললাম খাতায় ‘শুভ নববর্ষ’ লিখে সবাইকে পাঠাও। তখন সে নববর্ষের ‘নব’ অংশ লিখেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছে – তোমার বাবা নববর্ষে জন্মেছিলো নাকি? নবকুমার নাম? উত্তর ছিলো – না, নববর্ষে জন্মায়নি। নাম সংক্রান্ত কৌতূহল এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কিনা জানিনা! তবে আমার মতো তারও হয়তো প্রত্যেকবছর ‘নববর্ষ’ লিখতে গিয়ে দাদুর কথা মাথায় আসবে। আজ বাবা না থাকলেও, প্রতি ১ লা বৈশাখ আমি মন থেকে ১ লা হবো না। আমার প্রাণের মানুষ প্রাণেই থাকবেন।
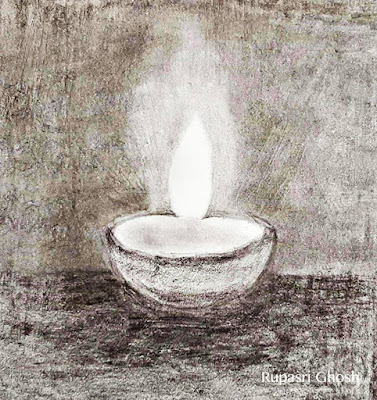
Comments
Post a Comment